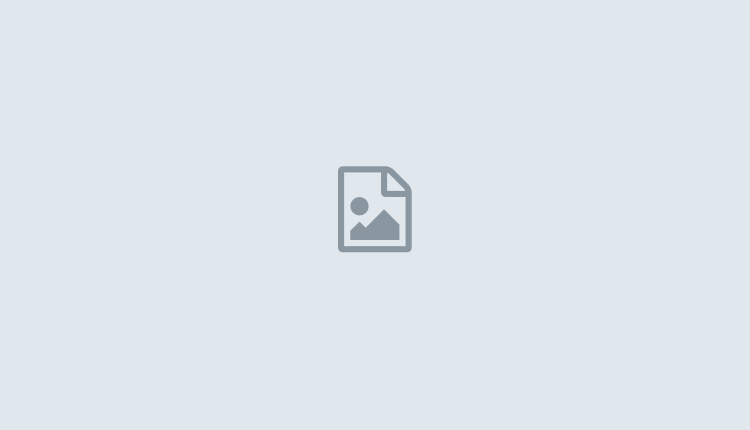সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়
কোভিড-১৯ এক ধরনের করোনাভাইরাস। অন্য করোনাভাইরাসগুলির সঙ্গে এই কোভিড-১৯-এর অনেক ফারাক রয়েছে। তাই অন্য করোনাভাইরাসগুলিকে চিনে, বুঝেও কোভিড-১৯-এর আচার, আচরণের পূর্বাভাস দেওয়াটা মুশকিল হচ্ছে। ফলে, কোভিড-১৯ ভাইরাস ঠিক কী ভাবে আমাদের শরীরে ঢুকবে, কোন কোন পথে ঢুকবে, বা তাকে রোখার চিকিৎসা ঠিক কী ভাবে সম্ভব, তার পূর্বাভাস দেওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আর সে জন্যই জীববিজ্ঞান কিছুটা গোলকধাঁধায় পড়ে গিয়েছে!
এই ক্ষুদ্র রাক্ষসগুলি কী ভাবে আমাদের আক্রমণ করে মোটামুটি ভাবে তার একটা ধারণা আমাদের আছে। কিন্তু সেই ধারণা কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের করোনাভাইরাসকে পুরোপুরি চেনা ও বোঝার কাজটা সহজ হচ্ছে না। যেহেতু এই ভাইরাস আমাদের অজানা, যেহেতু সব ধরনের কোভিড-১৯ ভাইরাস ও তাদের আচার, আচরণ সম্পর্কে আমরা এখনও ধোঁয়াশায় রয়েছি, তাই এদের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য আমাদের হাতে আসা প্রয়োজন। আগে তথ্য আসতে হবে প্রচুর পরিমাণে, তার পর সেগুলির বিশ্লেষণের কথা ভাবা যাবে।
এর পর আসি ‘ম্যাক্রো’ স্তরের প্রসঙ্গে। এই স্তরেও আমরা নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। তার ফলে, বিশাল জনসংখ্যায় এই ভাইরাস কী ভাবে ছড়ায়, ছড়ালে জনসংখ্যার কত জন সংক্রমিত হবেন, কত জন তাতে মারা যাবেন আর কত জনই বা সেরে উঠবেন, তা-ও সঠিক ভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না।
আগে তথ্য, পরে বিশ্লেষণ…
এখন আমাদের মুখে মুখে ঘুরছে কয়েকটা শব্দ। বা শব্দবন্ধ। আমরা আকছারই শুনছি, ‘কার্ভটা থমকে গিয়েছে’। মানে, বোঝাতে চাইছে, সেটা আর বাড়ছে না, কমছেও না। এও শুনছি, বলছি, ‘সংক্রমণের হার দ্বিগুণ হচ্ছে’।
এই সবই কিন্তু বলা হচ্ছে কয়েকটি তাত্ত্বিক মডেলের ভিত্তিতে। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমণের হার কী হতে পারে, তার একটা পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করে এই তাত্ত্বিক মডেলগুলি। এই মডেলগুলি কতটা নিখুঁত হবে, তা সর্বাধুনিক কম্পিউটার বা কোনও অ্যালগরিদমের উপর নির্ভর করে না। কত বেশি পরিমাণে কতটা নিখুঁত তথ্যাদি আমাদের হাতে আসছে, তার উপরেই নির্ভর করে তাত্ত্বিক মডেলগুলির সাফল্য।
তাই আবার বলছি, বেশি ও নিখুঁত তথ্যাদিরই প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তার পর আসে সেই তথ্যাদির বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ। তাই ভাইরাস কী ভাবে আমাদের শরীরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষগুলির মধ্যে কাজ করে আর কী ভাবেই বা তা লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংক্রমিত করে, তা সঠিক ভাবে বোঝার জন্য তথ্যাদির গুরুত্বই সর্বাধিক।
বস্তুত, জীববিজ্ঞানের প্রায় সব গবেষণার ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য। এটাই চলে আসছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, যত বেশি তথ্য তাঁদের হাতে আসবে, ততই তাঁরা সেই তথ্যাদি বিশ্লেষণের সুযোগটা পাবেন বেশি। পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁদের সুবিধাটা বেশি হবে। এটা যেমন কোনও সংক্রমণ ঠেকাতে আমাদের শরীরের প্রতিরোধী ব্যবস্থা কী ভাবে কাজ করে, সেটা বুঝতে সাহায্য করে, তেমনই বুঝতে সাহায্য করে মস্তিষ্কের কোন কোন জটিল প্রক্রিয়ার জন্য আমরা কথা বলতে পারি বা কোনও কিছু স্মরণে রাখতে পারি।
দ্রুত থেকে দ্রুততর ও উত্তরোত্তর উন্নত প্রযুক্তির দৌলতে বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি তথ্য আসছে। তথ্যের অপ্রতুলতার অভাব অনেকটাই মিটেছে। কিন্তু তার ফলে যে সব সময়ই জীববিজ্ঞানের কোনও জটিল রহস্যের জট খুলে গিয়েছে, কোনও তত্ত্বকে খতিয়ে দেখার পথ খুলেছে, তা কিন্তু নয়। যদিও এটাই হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।
জীববিজ্ঞানীরা এখন সেই সব তথ্য পেয়ে মনে মনে ভাবছেন, এটা বাড়ছে বা কমছে হয়তো অন্যটার প্রভাবেই। একটা কারণ হলে অন্যটা তার ফলাফল। তাঁরা কিন্তু সেটা ধরে নিচ্ছেন। সেটা পুরোপরি বা আংশিক সত্য না-ও হতে পারে।
পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাটা শুরু হয় তাত্ত্বিক মডেল থেকে
এ ক্ষেত্রে এখন জীববিজ্ঞানের গবেষণায় বিকল্প পথটা কী হতে পারে? পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় কী হয়, সেটা একটু ভাবা যাক। পদার্থবিজ্ঞানে শুরুটা হয় একটা তত্ত্বের পরিকাঠামো থেকে। সেই তত্ত্ব বা কোনও মডেল একটা পূর্বাভাস দেয়। পরে পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হয় তা প্রমাণিত হয় বা বাতিল হয়। বা তাকে কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন হয়। সেই ভাবেই গত কয়েক শতাব্দী ধরে পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশ ঘটেছে। হতে পারে, পদার্থবিজ্ঞানের কোনও তত্ত্ব বা কোনও মডেল কোনও প্রাকৃতিক ঘটনাকে পুরোপুরি সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। কিন্তু কী ভাবে গাণিতিক পদ্ধতিতে সেই সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তার একটা রাস্তা দেখাতে পেরেছে। পরে পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যাদি সেই তত্ত্বকে জোরালো করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয়। তখন ভাবনাচিন্তা শুরু হয় কোন পথ ধরে এগতে হবে, কোন কাজটা আগে করতে হবে, কোনটা পরে।
তাই তত্ত্ব আর পরীক্ষানিরীক্ষা, এই দু’টি হাতে হাত মিলিয়ে চললেই খেলাটা জমে ওঠে। ট্যাঙ্গো নাচ নিয়ে একটা প্রবাদ রয়েছে। দু’জনে ছাড়া ট্যাঙ্গো নাচা যায় না। ‘ইট টেক্স টু টু ট্যাঙ্গো’। বিজ্ঞানের গবেষণায় অনেকটা তেমনই।
ফ্রান্সিস ক্রিকের ‘মুশকিল আসান’ পদ্ধতি
ক্যালিফোর্নিয়ার ‘সল্ক ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে’ আমি নিউরোসায়েন্সে পিএইচডি করার সময় এই ব্যাপারটা খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম। বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিককে দেখেছিলাম। জিম ওয়াটসনের সঙ্গে যিনি ডিএনএ-র কাঠামো আবিষ্কার করেছিলেন। যা ছিল জীববিজ্ঞানের একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।
ক্রিক সল্ক-এ আমাদের গবেষণাগারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন। বিকেলে আমাদের ল্যাবরেটরিতে রোজ ‘চায়ের আড্ডা’য় থাকতেন উনি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওঁর সঙ্গে সেই সময় আলোচনা হত।
ছোট্ট একটা টেবিলের চার পাশে বসে আমরা আড্ডা মারতাম। তাতে নিউরোসায়েন্সের কোনও অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে জোর তর্কবিতর্কও হত। তার মধ্যে অন্যতম- চেতনার জন্ম কোথায়? কী ভাবে?
এ ক্ষেত্রে গবেষণার অনেক ঝুঁকি রয়েছে। কারণ, দার্শনিক থেকে শুরু করে মনস্তাত্ত্বিক বা সাধুসন্ত অথবা স্পিরিচুয়াল গুরু, সকলেরই এই বিষয়ে নিজস্ব মতামত আছে।
দেখেছিলাম, ফ্রান্সিস ক্রিকের একটা অদ্ভূত ক্ষমতা আছে। অনেকগুলি পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য থেকে কয়েকটিকে বেছে নিতে পারতেন। যার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপে পৌঁছনো যায়, সাধুসন্ত বা স্পিরিচুয়াল গুরুদের সঙ্গে কোনও বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়েও। ক্রিকের এই বেছে নেওয়ার মধ্যে যেটা অভিনবত্ব ছিল, সেটা হল, সেই পরবর্তী ধাপে আর অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার দরকার হত না। বরং যে সব তথ্য হাতে রয়েছে, সেগুলি থেকেই কোনও প্রামাণ্য ধারণায় পৌঁছনো যায় কি না, তার চেষ্টা করতেন ক্রিক।
অবশ্যই এই ভাবে এগনোর অনেক ঝুঁকি আছে। অভিজ্ঞতা বলে, ব্যর্থতার হার কম নয়। যেমন ভাবা হয়েছিল, ফলাফল খুব কম ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে মেলে। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানের গবেষণায় তাত্ত্বিক বলে পরিচিত, তাঁরা পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু ভুল প্রমাণিত হল কি না, তার তোয়াক্কা করেন না। তাঁরা যেমন ‘প্রচুর তথ্য হাতে নেই’ বলে আক্ষেপ করেন না, তেমনই ‘প্রচুর তথ্য হাতে আছে’ বলে উৎফুল্লও হন না। তাঁরা তত্ত্ব দিয়ে একটা ধারণা তৈরি করেন, যা পরে পরীক্ষায় প্রমাণ করা যেতে পারে। আবার না-ও পারে। তাই কোনও সত্যে উপনীত হওয়ার আগে বহু তত্ত্বের জন্ম হয়, নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষারও প্রয়োজন হয়।
জীববিজ্ঞানে অগ্রাধিকার তথ্যের, তার পর তৈরি হয় তত্ত্ব
কিন্ত যে জীববিজ্ঞানীরা মূলত পরীক্ষানির্ভর গবেষণা করেন (‘এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজিস্টস’) তাঁরা কোনও বিশ্লেষণ শুরুর আগে হাতে প্রচুর তথ্য পেতে চান। তার ফলে, কখনও কখনও কোনও পরীক্ষানির্ভর জীববিজ্ঞানীর হাতে এত তথ্য এসে যায় যে, সেখান থেকে কোন তথ্যাদি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর কোন কোন তথ্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তা বুঝে ওঠাটাই সেই জীববিজ্ঞানীর পক্ষে মুশকিল হয়ে ওঠে। তত্ত্ব আর পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা আর তার মিশেল ঘটানো, সংস্কৃতির নিরিখে, এই দু’টো জিনিসই পদার্থবিজ্ঞান আর জীববিজ্ঞানের গবেষণাকে আলাদা করে দেয়।
আরও একটা ফারাক আছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে মোটামুটি ভাবে তাঁর বিচক্ষণতা দিয়ে একটা প্রাথমিক অনুমান (‘ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন’) করে নিতে পারেন। তাতে হাতে প্রচুর তথ্য না থাকলেও গবেষণাকে কিছুটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। পরীক্ষানিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ থেকে পরে যত তথ্য এসে পৌঁছয়, ততই মঙ্গল। তা কোনও তাত্ত্বিক পূর্বাভাসকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। কিন্তু জীববিজ্ঞানের অধিকাংশ গবেষণাতেই আগে লাগে তথ্য। তার পর সেগুলি নিয়ে ভাবা শুরু হয়।
দু’টি ভিন্ন সংস্কৃতি, বিরোধ নেই, এগয় আলাদা পথে
তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, তত্ত্ব ও পরীক্ষানিরীক্ষাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞান আর পদার্থবিজ্ঞানের দু’টি আলাদা সংস্কৃতি কী জিনিস?
এটা এমন নয় যে, দু’টি সংস্কৃতির মধ্যে একটা অন্যের চেয়ে ভাল। তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ রয়েছে, এমনও নয়। কোনও একটি সমস্যার সমাধানে দু’টি সংস্কৃতি আসলে দু’রকম ভাবে এগয়।
কিন্তু এই সংস্কৃতির ফারাকে কি সত্যিই কিছু এসে যায়? আমাদের সভ্যতার অস্তিত্ব নানা কারণে দিনকে দিন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে। তাই বিজ্ঞানের কোনও একটি শাখার পক্ষে সভ্যতাকে সেই সঙ্কট থেকে বের করে আনা সম্ভব নয়।
নিছক হ্যান্ডশেক নয়, প্রয়োজন দু’টি সংস্কৃতির মেলবন্ধন
করোনা সঙ্কট মনে করিয়ে দিল, এই দু’টি ভিন্ন সংস্কৃতিকে এ বার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। এক দিকে, তাত্ত্বিক মডেল দিয়ে বুঝতে হবে, এই ভাইরাস কী ভাবে আমাদের শরীরে ঢোকে, কোন কোন পথে ভাইরাসটি আমাদের আক্রমণ করে। অন্য দিকে, এই ভাইরাস কেন এতটা সংক্রামক, কেন এতটা ক্ষতিকারক, শুধু সেটা বুঝলেই হবে না; বুঝতে হবে কেন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন জনসংখ্যার উপর এক প্রভাব আলাদা আলাদা।
আবার হাতে প্রচুর তথ্য এলেও হবে না। তথ্যাদি জোগাড় করতে হবে তত্ত্বগুলিকে মাথায় রেখে। আর সেটা করলেই আমাদের নতুন বোধোদয় হবে। যা অন্য কোনও উপায়ে সম্ভব নয়।
সেটা একমাত্র সম্ভব দু’টি ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনেই। যা শুধুই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির ‘হ্যান্ডশেক’ নয়। হবে আক্ষরিক অর্থেই, একটি মেলবন্ধন।